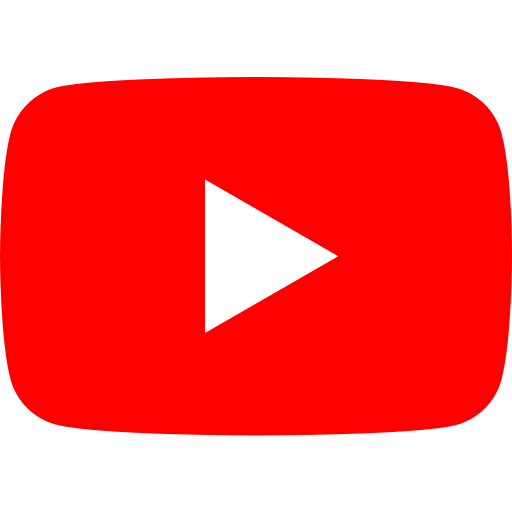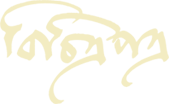রোগাটে, লম্বাটে, আড্ডাবাজ, কিঞ্চিৎ সুখাদ্য ও খোলা সিগারেটের টিন সামনে পেলেই মুহূর্তে কিলিমানজারো থেকে কামস্কাটকা হয়ে মঙ্গলগ্রহ অবধি পৌঁছে যেতে তাঁর মগজ-যানকে কদাপি বিদেশি সাইফির থিমট্যাঙ্ক থেকে জ্বালানি ভরবার জন্য দাঁড়াতে হয় না। বরং মহাকাশের ফুটো থেকে অফুরান এনার্জির খবর তাঁর ট্যাঁকে গোঁজা থাকে।এহেন ঘনশ্যাম দাস উর্ফ ঘনাদা বাঙালির বুকের একেবারে কাছটিতে বসবাস করেন। ঘনাদাকে জানেন না এমন পড়ুয়া বাঙালি ক’টি আছেন হাতে গুণে বলা যাবে।
এই গভীর ভালোবাসার দিকটা কিন্তু সত্যিই অবাক করা। একে তো বাংলা সাহিত্যের পাঠকের মূলধারা তথাকথিত খানদানি ‘সাইফাই’ দেখলে, ইয়ে…খানিক হাই তোলেন বলে বদনাম। তার ওপর লেখকের ব্যক্তিগত ক্যারিজমা, যে জিনিসটা বাংলা সাহিত্যের আরেক মৌলিক সম্পদ প্রফেসর শঙ্কুর জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে বেশ খানিক থেকেই যায়, তার বিশেষ উপস্থিতি এ-ক্ষেত্রে নেই। তাহলে?
ঘনাদা বিষয়ক
বাংলার সাহিত্যজগতে ১৯৪৫ সালে আবির্ভাব। এবং ভিনি ভিডি ভিসি। তারপর থেকে বছরে বছরে আমাদের ঘনাদার শ্রীমুখনিঃসৃত সুদীর্ঘ অ্যাডভেঞ্চারমালা বাঙালিকে কিলিমানজারো থেকে মঙ্গলগ্রহ হয়ে এভারেস্টের মাথায় কি সমুদ্রের তলায় সর্বত্র টেনে নিয়ে গেছে অক্লেশে। শুনেছি ব্ল্যাক হোল থেকে এনার্জি বের করবার স্বপ্ন থেকে শুরু করে উড়ন চাকতির বা ওয়ার্ম হোলের কাহিনী। আবার কখনো মহাভারতের পাতা থেকে পেরুর আদিম সভ্যতার বুকে গাইডেড ট্যুর হয়েছে আমাদের তাঁর বা তাঁর পূর্বপুরুষদের কল্যানে।
ঘনাদার স্রষ্টা গত হয়েছেন তা ও অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেল। ঘনাদা কিন্তু সমান প্রতাপেই বর্তমান পাঠকের বুকশেলফে। কোন জাদুতে তা সম্ভব হল সেইটিকে বুঝতে হলে প্রথম কিঞ্চিৎ ভূমিকা প্রয়োজন হবে।
দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় লেখাগুলোকে। একটি দলে রয়েছে বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কাহিনী। অন্যদিকে ইতিহাস। দুটি ধারাতেই সাধারণ উপস্থিতি রয়েছে ঘনাদার প্রকট চালবাজি এবং তাঁর বা তাঁর পূর্বজের কোন দুঃসাহসীক অ্যাডভেঞ্চারের উপাদান।
সায়েন্স ফিকশান??
বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে সাহিত্যচর্চার ধারা বাংলা সাহিত্যে বড়োই দুর্বল হওয়াতে (আজ্ঞে হ্যাঁ, সোনালী সত্তর ইত্যাদি অস্থায়ী উত্থান সত্ত্বেও) সাধারণত সায়েন্স এবং ফিকশান একত্রে থাকলেই এ-ভাষার পাঠক সে লেখাকে যাহা সায়েন্স তাহাই ফিকশন দ্বন্দ্ব সমাস এই বিচারে সায়েন্স ফিকশান আখ্যা দিয়ে থাকেন। এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কল্পনাকে বিজ্ঞানের আগে স্থান দিয়ে তার বাংলা নামকরণ করে দেন কল্পবিজ্ঞান। ঘনাদার বিজ্ঞাননির্ভর গল্পগুলোও এইভাবে সাধারণভাবে কল্পবিজ্ঞানের আখ্যা পেয়ে চলেছে বারংবার বিভিন্নজনের কলমে।
বিজ্ঞান নিয়ে তিনটে ধারার ফিকশান রচিত হয় মূলত। প্রথমটি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও আবিষ্কারের উপযুক্ত প্রয়োগ করে সেখানে কাহিনিশরীর গড়ে তোলা হয়। সমসময়ের যুক্তিনির্ভর ও বাস্তব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সে-গল্পের একটি প্রধান উপাদান হয়ে আসে। দ্বিতীয় ধারায় আসবে প্রফেসর শঙ্কুসদৃশ গল্পগুলি, যেখানে বিজ্ঞান আসলে এক ইচ্ছাসুখে বিস্ময়সৃজনের জাদুদণ্ডমাত্র। বিজ্ঞানের ‘লজিকাল এক্সটেনশান’ সেখানে ব্যাকসিটে। শ্মশানের কাছে পাওয়া গাছের শেকড়ের রস সেখানে ভূত দেখবার যন্ত্র আবিষ্কারের অনুপান হয়ে ওঠে। একে বলতে পারি বিজ্ঞানসুরভিত ফ্যান্টাসি। তৃতীয় ধারায় রয়েছে প্রকৃত কল্পবিজ্ঞান। সায়েন্স ফিকশান প্রকাশনায় দুনিয়াতে অগ্রগণ্য পত্রিকা ‘অ্যানালগ’এর দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী এই ধরণের গল্পে থাকতে হবে কল্পিত ভবিষ্যতের বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির ব্যবহার। এবং তা এমনভাবে প্রযুক্ত হতে হবে যাতে তাকে বাদ দিয়ে গল্পটার অস্তিত্ত্ব সম্ভব না হয়। (উদাহরণস্বরূপ তাঁরা মেরি শেলির ফ্রাংকেনস্টাইন গল্পটিকে দেখিয়েছেন।) এই ভবিষ্যবিজ্ঞান হতে পারে ভৌত, সমাজতাত্ত্বিক কিংবা মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি, কিংবা তাদের মিশ্রণ। সর্বোপরি, গল্পে যে ভবিষ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ হবে তাকে বিশ্বাসযোগ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য হতে হবে।(যথা অতি-আলোকগতি ইঞ্জিন। কল্পিত, কিন্তু বর্তমান মহাকাশ ইঞ্জিনপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের একটি যুক্তিগ্রাহ্যভাবে প্রসারিত ভবিষ্যকল্পনা) দিলীপ রায়চৌধুরীর গল্পগুলো এবং অদ্রীশ বর্ধনের প্রফেসর নাটবল্টুচক্র সিরিজের বেশ কিছু গল্পকেই এই শ্রেণীতে ফেলা যায়।
ঘনাদার অজস্র গল্পের মধ্যে কিছু সংখ্যক গল্পেই কিন্তু প্রকৃত কল্পবিজ্ঞানের স্পর্শ আছে। যেমন ‘ফুটো’। চতুর্থমাত্রাভেদি ওয়ার্ম হোলের ব্যবহার করে মুহূর্তে মঙ্গলগ্রহে পৌঁছে যাওয়ার যন্ত্রের ব্যবহার করা হয় সেই গল্পে। এছাড়া লাট্টু আর মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা এই দুই গল্পেও সেই স্পর্শ পাওয়া যায়। এমন কিছু কিছু কাহিনি ছাড়া ঘনাদার অন্যান্য বিজ্ঞানসম্পর্কিত গল্পগুলোকে কল্পবিজ্ঞান বলাটা অনুচিত হবে। এগুলোকে বরং বাস্তব কিংবা কল্পিত বিজ্ঞাননির্ভর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি বললে এদের ওপর সুবিচার করা হয়।(উদাহরণঃ মশা গল্পটার কথা ধরুন। ওখানে বিজ্ঞানের কল্পিত অবদান সেই ভয়ানক মশার বদলে একটি পাহাড়ি কাঁকড়াবিছে ছেড়ে দিলেও গল্পটা দিব্যি দাঁড়িয়ে যেত।)
এর প্রতিটি কাহিনিতে জানা অজানা হরেক তথ্যের স্রোত অ্যাডভেঞ্চারের রসে জারিত হয়ে পাঠকের মনোজগতে এসে পৌঁছোয়। প্রাক ইন্টারনেট যুগে, বিচিত্র জ্ঞানের ভান্ডারটা যখন আমজনতার আঙুলের ডগায় আর মোবাইল ইন্টারনেটের পর্দায় এমনভাবে এসে দাসখত লিখে দেয়নি, সেই সময়ে বিজ্ঞান, ভূগোল, পরিবেশ, বিশ্বরাজনীতির ব্যাপারে এমন সুস্বাদ ও দুর্লভ এক্সপোজার বাংলা সাহিত্যে আর কোন গল্পমালা দিতে সক্ষম হয়নি তার পাঠককে। ঘনাদার সেসময়ের বিপুল জনপ্রিয়তার একটা কারণ হিসেবে একে সহজেই ধরে নেয়া যায়।
কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যায়। ইন্টারনেটের আগমন সত্ত্বেও ঘনাদার জনপ্রিয়তা একই জায়গায় রয়ে গেল কোন রহস্যে?
একটা কারণ, তবে একমাত্র নয়
তবে, শুধুমাত্র বিচিত্র তথ্যাদির সুস্বাদ অ্যাডভেঞ্চারগন্ধী পরিবেশন যদি এর জনপ্রিয়তার একমাত্র কারণ হত তাহলে আজ যখন মিডিয়া ও প্রযুক্তির বিপ্লবের ফলে দুনিয়া সম্বন্ধে যাবতীয় বিচিত্র তথ্য সস্তা ও সহজলভ্য হয়ে উঠেছে এবং অ্যাডভেঞ্চারধর্মী অজস্র পাঠ্য ও দৃশ্যশ্রাব্য উপাদান কেবল টিভি, চলচ্চিত্র ও বইয়ের মাধ্যমে বঙ্গভাষীর হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে তখনও ঘনাদার জনপ্রিয়তা বাঙালি পাঠকমহলে এত অপ্রতিরোধ্য থাকত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটা সেইরকমই ঘটেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের পাঁক বা মহানগর ক’জন পড়েছেন বা মনে রেখেছেন তাঁর লেখা হিসেবে তার সঙ্গে ঘনাদার কজন ভক্ত আছেন বাংলায় সে তুলনাটা করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।
কাজেই ধরে নেয়া যায় এ গল্পগুলোয় নিশ্চয় জনপ্রিয়তার অন্য কোন উপাদান রয়েছে যা তখন এবং এখন এই দুই সময়েই পাঠককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম। বা, অন্যভাবে বললে, এমন কোন সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার অনুসন্ধান করা যেতে পারে, যার প্রভাবে ঘনাদার গল্প বয়স নির্বিশেষে বাঙালিকে বেজায় নাড়া দিতে পেরেছিলো তার আবির্ভাবকালে। এর পর যদি অনুসন্ধানে দেখা যায় যে সেই সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা এখনো বাঙালির রয়েছে তাহলে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে গল্পের সেই উপাদানটিই তাকে ধারাবাহিক জনপ্রিয়তা দিয়ে চলেছে সেই ১৯৪৫ থেকে আজ ২০১৯ সালেও।
উপপাদ্যটাকে বুলেটবন্দি করলে এইরকম দেখাবে–
ক। ঘনাদার আবির্ভাবকালে বাঙালির সমাজ ও মনোজগতের অবস্থাটা ঠিক কেমন ছিল?
খ। অজানা জ্ঞানবিজ্ঞান ও অ্যাডভেঞ্চাররস ভিন্ন ঘনাদার গল্পগুলোর দ্বিতীয় কোন উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য আছে কিনা যা সেই সময়কার বাঙালি সমাজ ও মনোজগতের গল্পগুলোকে জনপ্রিয় করে তোলবার পেছনে দায়ী ছিল?
গ। সেই সামাজিক ও মানসিক পরিবেশগত কারণটি এখনও উপস্থিত কি না।
ঘনাদার আবির্ভাবকালে বাঙালির মনোজগত ও সমাজ
পাণ্ডববর্জিত বঙ্গভূমি চিরকালই আর্যাবর্তের একটেরেতে কিঞ্চিত হেলাফেলায় পড়ে থাকা একটি ভূখণ্ড থেকে গেছে। পালযুগে খানিক গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে হাত পা ছড়ানো, কিংবা একজন চৈতন্য মহাপ্রভুর ভাগবত দর্শনের ওপরে উল্লেখনীয় অবদান, এইরকম কিছু ব্যতিক্রমী কাল ও ঘটনা বাদে ভারত কিংবা বিশ্বের ইতিহাসে তার নামডাক বিশেষ শোনা যায় না।
সাদাসিধে, বেশ খানিক ভিতু, ব্যবসাবুদ্ধিতে পিছড়ে বর্গ, রণক্ষেত্রে গোত্রহীন এই লতাচরিত্র মিশ্রিত জাতিটির কপাল কিছুকালের জন্য খুলে গিয়েছিল উনিশ শতকে ইংরেজের আবির্ভাবে। তাদের সাদর প্রশ্রয়ে শিক্ষিত চাকুরি ও পেশাজীবি মধ্যবিত্ত একটি শ্রেণী গড়ে তুলে এই জাতি এ দেশে তাদের সাম্রাজ্যবিস্তারে কনিষ্ঠ লক্ষণহেন নীরব সেবাদান করেছে। তার রেনেসাঁর মাধ্যমে এদেশে ইংরিজিবিদ্যায় শিক্ষিত বৃটিশ শাসনের ও বৃটিশ ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলির স্তম্ভস্বরূপ বিশ্বস্ত কেরাণিকূল গড়ে তুলেছে।
১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে ইংরেজের অধিকার বজায় রাখবার ব্যাপারে তার একমাত্র অস্ত্র কলমটিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছিলেন বাঙালি ইন্টেকচুয়ালকূল। তার পুরষ্কারস্বরূপ বিশ্বস্ত সেবকজাতি হিসেবে সাহেবের আশীর্বাদ অর্জন ছিল এর অন্যতম সুফল। পাশাপাশি অনুকূল-মনস্ক অ্যাবসেন্টি জমিদারকূল ও ‘কমপ্রাদর বুর্জোয়া’ শ্রেণীটিও আত্মস্বার্থেই বৃটিশ শাসনকে সাহায্য করে যাবার ব্যাপারে অকথিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছিলেন।
এর বিনিময়ে উনিশ শতকের শুরুর দিক থেকে ক্রমপ্রসারমাণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে বেশ কিছুটা সময় জুড়ে রাজার পেয়াদা হিসেবে তার বেজায় হাঁকডাকও হয়েছিল। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তখন সে যা বলে তাই এদেশের নেটিভের কাছে গুরুবাক্য। জন্ম নিয়েছে সেই বিখ্যাত প্রবচন, হোয়াট বেঙ্গল থিংকস্ টুডে, ইন্ডিয়া উইল থিংক টুমরো। এ-সময়টা বাংলার ইতিহাসে তাই বেজায় গৌরবময় কাল বলে গণ্য করা হয়।
এই পর্যায়ে বাঙালির কপাল পোড়ার শুরুয়াত হল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে এসে। সারা দেশে তার বেজায় প্রতিপত্তি যে কতোটা বৃটিশ সহায়তানির্ভর সে-আন্দাজ ভুলে গিয়ে সে আত্মশক্তিতে ‘বলীয়ান’ হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনে রাস্তায় নেমে পড়ল। কবি-সাহিত্যিকরা রাজনৈতিক আন্দোলনের তত্ত্বসৃজন ছেড়ে তার বাস্তব প্রয়োগের নেতৃত্ব দখল করলে যা হয় আর কি। আদর্শে, তাত্ত্বিক জ্ঞানে একশোয় সোয়াশো, বাস্তবজ্ঞানে মাইনাস পাঁচ।
বিশ্বস্ত অনুচরের এহেন আকস্মিক বীরত্বের প্রকাশে খানিক নাস্তানাবুদ হয়ে শ্বেতাঙ্গ শাসককূল বঙ্গভঙ্গ রদ করল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে তোল্লাই পেয়ে বাড় বেড়ে যাওয়া জাতিটিকে পুনর্মুষিক বানাবার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাদের রাজধানীকে সরিয়ে নিয়ে গেল কলকাতা থেকে দিল্লি। শুরু হল পতন। বেড়ালের বিয়েতে চাষীশোষা পয়সা ওড়ানো বীর বাঙালির নকল আর্থিক পেশিকে তুচ্ছ করে দিয়ে শিল্পে সামনে উঠে এল পশ্চিম উপকূল, বৃটিশ শাসকের কেন্দ্রিয় শক্তিস্থল দিল্লিতে সরবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির ময়দানে পুরোনো খেলোয়াড়,মূল আর্যাবর্তের লোকজন, এ-দেশের প্রকৃত রাজনৈতিক শক্তির গদিটা থেকে হেলায় বাঙালিকে বিদেয় করে জুড়ে বসল ও দেশ থেকে বৃটিশবিদায়ের আন্দোলনের রণকৌশলের নির্ধারক হয়ে বসল। ময়দানে নামলেন গান্ধিজি, ধুরন্ধর কাশ্মিরী পণ্ডিতকূল এবং অন্যান্যরা।
চল্লিশের দশক এল যখন, ততদিনে বাঙালি আবার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সেই পুরোনো তিমিরে ফিরে গেছে।
তেতাল্লিশে, বিশ্বযুদ্ধের বাজারে যখন বর্মা থেকে চাল আসা বন্ধ, এই প্রদেশের উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্যও ডাকাতি হয়ে গিয়েছে বিশ্বযুদ্ধের সেপাইদের পেট ভরাবার জন্য, সেই কৃত্রিম আকালের সময়ে, এককালের পেয়ারের সেবক জাতটির পেট ভরাবার জন্য কানাডার খাদ্য-সহায়তাদানের প্রস্তাব তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিলেন উইন্সটন চার্চিলের সরকার। ত্রিশ লাখ বাঙালি মারা পড়ল সে বছর। স্রেফ না খেয়ে। বাকি ভারত একটা আঙুলও তুলল না।(এ-বিষয়ে মধুশ্রী বসুর “চার্চিলস্ সিক্রেট ওয়ার” নামের বইটা দেখতে পারেন উৎসাহী পাঠক)
জাত হিসেবে এই চরম অবমাননা আর চূড়ান্ত কষ্ট থেকে লড়াই করে বের হয়ে আসবার মত মেরুদন্ডের জোর এই নরগোষ্ঠীর ছিল না। তার সমাজের নিচের তলার মানুষেরা তাই মরতে মরতেও কোনক্রমে বেঁচে রইল। বেঁচে থাকবার প্রত্যক্ষ যন্ত্রণা তার এত তীব্র যে দেহ আর প্রাণটুকু একত্রে ধরে রাখা ছাড়া তার আর কোন অনুভূতি নেই। অতএব তারা কোনমতে দেহ ও প্রাণকে একত্র রেখে পরবর্তী অবমাননা ও মৃত্যুস্রোতের বলি হবার জন্য তৈরি হতে থাকল।
কিন্তু সমস্যায় পড়লেন বাংলার নাগরিক, শিক্ষিত ইন্টেলেকচুয়ালকূল। ইতিহাসের জ্ঞান তাঁদের আছে। চাষাভুষোর তুলনায় জীবনের কিঞ্চিত অধিক নিরাপত্তা থাকায় সেদিকে চোখ ফেলে দেখবার খানিক অবসরও আছে। মাত্রই কিছুকাল আগে এ-দেশের সমাজের সর্বস্তরে সেরা জাতির শিরোপাটা যে তাঁদের ঠিক আগের প্রজন্মের মাথায় ছিল সে-স্মৃতিও তাঁদের মনে জ্বলজ্বল করে সর্বদাই। সাহেবের পেয়াদার চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া ও তারপর দেশিবিদেশি সকল বেরাদরের হাতে ক্রমাগত লাঞ্ছিত হয়ে চলা ও তার প্রতিকার করবার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক-রাজনৈতিক শক্তি এবং (লতাচরিত্র হবার দরুন) সৈনিকসুলভ উদ্যমের একান্ত অভাব, এই সবকিছু মিলে বৃহত্তর বাঙালির এই উপজাতিটি তখন বেজায় মানসিক চাপে। যন্ত্রণা এবং তার থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার অক্ষমতার ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান, এই দুয়ে মিলে তখন তার দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।
কথায় বলে দেয়ালে পিঠ ঠেকলে বেড়াল দাঁতনখ বের করে। কিন্তু যে বেড়ালের দাঁতনখ নেই, বাবুরাম সাপুড়ের পুষ্যিহেন সেই বেড়াল তবে দেয়ালে পিঠ ঠেকলে কী করে?
মনোবিদরা বলেন, অত্যধিক মানসিক যন্ত্রণা যখন কেউ সহ্য করতে পারে না, এবং তার প্রতিকারও তার সাধ্যাতীত থাকে, তখন মন একটা কল্পনার অবাস্তব দুনিয়া তৈরি করে তার ভেতরে সেঁধিয়ে যায়। নাগরিক ও আধা নাগরিক ইন্টেলেকচুয়াল বাঙালি অতএব সেই মনোরোগের অন্ধকারে তলিয়ে গেল। কঠোর বাস্তবমুখি সৃজনশিল্পের কিছু প্রচেষ্টার পাশাপাশি বাংলা চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, সাহিত্য সর্বত্রই একটা অসঙ্গত রোমান্সের জোয়ার এল। প্রেম-ভালোবাসা, গাঁয়ের বধু, বিপ্লব, মেকি রিয়েলিজম, সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা মখমলি ড্রেসিং গাউনের ছবি বিশ্বাস, চুলে সিঙাড়া ললিপপ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার নায়ক কিংবা ঢলো ঢলো (একটু মোটার দিকে) নায়িকাশ্রেষ্ঠারা ভিড় জমালেন তার বইয়ের পাতায়, সিনেমার পর্দায়। তার সঙ্গীতশিল্পে তখন বাংলার সেরা আধুনিক রোমান্টিক গানেরা জন্ম নিচ্ছে।
বাঙালির এই দুর্দশাগ্রস্ত ও মনোরোগীসুলভ জীবনযাত্রার পটভূমিতেই ঘনাদার আবির্ভাব। ১৯৪৫ সনে। দেব সাহিত্য কুটিরের এক পূজাবার্ষিকীতে। পাঁক, শুধু কেরাণি, ফেরারি ফৌজ, মিছিল-এর শ্রেণির সাহিত্যস্রষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ততদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যদর্শন থেকে বিপরীতমুখে ঘুরে গিয়ে সৃষ্টি করলেন ঘনাদার। প্রাকবিশ্বযুদ্ধকালহেন শান্তিরও খানিক সচ্ছলতার অলীক পরিমণ্ডলে, অলস জীবনযাত্রায় অধিষ্ঠিত একজন অবিবেকি, মিথ্যাচারী, চালবাজ মানুষ এই ঘনশ্যাম দাস। সে তার অতীত গরিমা নিয়ে কল্পনার গল্প ফেঁদে সম্মান, সুখাদ্য ও নেশাদ্রব্যের সংগ্রহ করে থাকে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি নগরবাসী সেই ভয়াবহ অনিশ্চয়তার ও দুঃখের সময়ে উদ্ভট, অলীক কল্পনায় মোহিত হবার সুযোগ পেতেই তাকে দু’হাতে আঁকড়ে ধরে নিজের কাছে রাখতে চাইল বিনোদনের উপকরণ হিসেবে। অতএব, আবির্ভাবমুহূর্তে বনমালী নস্কর পথের মেসটিতে হাজির হওয়া চালচুলোহীন অপরিচিত লোকটি যখন উদ্ভট এক গল্প শুনিয়ে সেখানে আশ্রয় যাচনা করেন, তখন, লন্ডন টাইমসে জার বোয়া ছাপ মারা বিজ্ঞাপনের জবাব আসবার জন্য অপেক্ষা করতে মেসের তরুণ বাসিন্দারা অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁকে আশ্রয় দিয়ে ফেলে তাদের টঙের ঘরে। সে-সময়কার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাঙালির প্রতিভূ এই মেসবাসীরা চাকরি-বাকরি, চাকরির সন্ধান, গল্পগাছা, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল নিয়ে দিব্যি মজে আছে। দেশের উত্থানপতনে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।
জ্ঞানবিজ্ঞান ও অ্যাডভেঞ্চার ভিন্ন ঘনাদার গল্পের তৃতীয় রস
ঘনাদার গল্পগুলো একটু খেয়াল করলে দেখবেন, গল্পের মূল যে প্রতিপাদ্য সেটা গল্পের প্রথম কয়েকটা পাতা বাদ দিয়ে শুরু করলেও স্বচ্ছন্দে উপভোগ করা যায় বিশেষ কোন খেই না হারিয়েই। প্রায় প্রতিটি গল্পের মধ্যেই দুখানা অংশ রয়েছে। একটা অংশ ঘনাদার অ্যাডভেঞ্চার। সেটা গল্পের মাঝখানটা। সেই অংশে ঘনাদা একজন আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ নায়ক। তিনি তীক্ষ্ণধী, বাগ্মী, প্রবল জ্ঞানী, অতুলনীয় রণকুশলী, জীবনমৃত্যুকে তোয়াক্কা না করা, প্রত্যুৎপন্নমতি, সৎ, মানবিক, জাতিভেদবিরোধী, পরিবেশ সচেতন, কূটনীতিক, ওয়েল কানেকটেড এবং একেবারেই দারিদ্র্যহীন একজন আদর্শ হিরো। জুল ভার্নের অ্যাডভেঞ্চার, বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞান সুরভিত কাহিনিগুলোর বহু নায়কের চরিত্রের সঙ্গেই তাঁর মিল আছে। সাইরাস হার্ডিং, নিমো, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এঁদের কথা মনে করে দেখুন।
কিন্তু জুল ভার্নের বিপরীতে গিয়ে, এই অংশটাকে রিয়েল টাইমের অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে না দেখিয়ে লেখক এটিকে দেখাচ্ছেন একজন মানুষের বলা ন্যারেটিভ হিসেবে। এশিয়ান সাহিত্যের এই চিরায়ত ন্যারেটিভ স্টাইলে গল্পটা রিয়েল টাইমে ঘটে না। কোন কথকের ভাষায় হিসেবে তা পাঠকের বা শ্রোতার সামনে পেশ করা হয়। এই ধারা মহাভারত থেকে সমানে চলে আসছে আমাদের দেশিয় সাহিত্যে। এদেশি ভাষার পাঠক এ স্টাইলে অভ্যস্ত। বিদেশি গল্পকথনের ইমার্সিভ স্টাইল যাতে ঘটনা পাঠকের সামনে রিয়েল টাইমে ঘটতে থাকে ও একসময়ে সেলফ আইডেন্টিফিকেশানের ফাঁদ পেতে পাঠককেও তার মধ্যে জড়িয়ে ফেলে একেবারে, সে-পদ্ধতি ঘনাদার অ্যাডভেঞ্চারে নেই।
এখন, এই মাঝখানটাই স্বচ্ছন্দে সম্পূর্ণ গল্প হতে পারত তার হুল ফোটানো ল্যাজা আর প্রায়শ প্রবল লম্বা, ভারী ও বিরক্তিকর মুড়োটা বাদ দিয়ে। কিন্তু এ-গল্পগুলোতে তা কখনোই হয় না। ঘনাদার গল্পের দ্বিতীয় অংশটা, যার উপস্থিতি গল্পের ল্যাজা আর মুড়োয় তা সবসময়েই এ-গল্পদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকে।
সেইখানেও মধ্যমণি সেই ঘনাদাই। কিন্তু এখানে তিনি একজন ব্যর্থ, দরিদ্র, কখনো কখনো পাওনাদারের হাতে লাঞ্ছিত মানুষ। মাথার জোর তাঁর আছে। পড়াশোনাও গভীর। কখনও কখনও, সম্ভবত নতুন করে রসদ সংগ্রহের প্রয়োজনেই তিনি চুপ মেরে যান আর সে নীরবতা ভাঙে নতুন একটি অসাধারণ তথ্যসমৃদ্ধ ও বিজ্ঞান-সুরভিত অ্যাডভেঞ্চারের গল্পে, যে-গল্পের কেন্দ্রে থাকেন তিনি নিজে, অরণ্যদেবসুলভ হৃদয়, দেহ ও বিবেক নিয়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে।
সেই মূল গল্পে দেখি, বারংবার তিনি শিকার হয়ে চলেন তুলনায় শক্তিশালী কোন জাতের মানুষের হাতে, কখনো কালো নেংটি, কখনো বা চিমসে ভিখিরি উপাধিতে ভূষিত হয়ে। এবং তারপর হঠাৎ চেহারার তুলনায় অপ্রত্যাশিত বীরত্ব প্রদর্শন করে অক্লেশে কাত করে ফেলেন সেই শক্তিমান জাতির প্রতিভূকে যে নাকি তাঁকে অপমান করেছিল নিজের শক্তির গর্বে। বাস্তবে যে সম্মান উদ্ধার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব, কল্পনায় তাকে তিনি জয় করে নেন। অস্তিত্ত্বরক্ষার কারণ খুঁজে নেন বাস্তবের দুনিয়া ছেড়ে নিজেকে হ্যালুসিনেশানের কল্পজগতে গুটিয়ে নিয়ে।
নিজের দুঃসহ, সর্বার্থেই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত বর্তমানকে উপেক্ষা করবার জন্য তিনি কল্পনায় গড়ে তুলেছেন এক বর্ণময়, উজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্যের কল্পকাহিনি, যে কাহিনিতে বাস্তব ইতিহাস-ভূগোল এবং কল্পিত বিজ্ঞান হাত ধরাধরি করে এগোয়, যার মিথ্যেটা তিনি ভালো করেই জানেন, আর সেইসঙ্গে জানে তাঁর কথা যারা শুনছে তারাও। উইলফুল সাসপেনশান অব ডিজবিলিফের আফিমের নেশায় আচ্ছন্ন কথক ও শ্রোতা কিছুক্ষণের জন্যে নিজের জীবন নিয়ে ফ্যান্টাসাইজ করে ফের বাস্তবের দুনিয়ায় ফিরে আসেন, স্রেফ আফিমের পরের ডোজটির জন্য অপেক্ষা করতে।
চিরকেলে পিছড়ে বর্গের বাঙালি, উনিশ শতকের বৃটিশ যুগে তাদের সাম্রাজ্যবিস্তার ও রক্ষার সহায়ক হবার পুরস্কার-স্বরূপ একরাতের রাজা হয়ে নিজেকে ভারতভূমিতে কাল্পনিক উচ্চাসনে বসিয়েছিল। সেইখান থেকে রূঢ় বাস্তবের গুঁতোয় বিচ্যূত হবার পর নিদারুণ এক যন্ত্রণার সময়ে সে নিজের অতীতটাকে একটা সাংঘাতিক উঁচু কিছু ভেবে নিয়ে তার অসত্যতা সম্পর্কে অন্তরে সচেতন হয়েও নিজেকে ডুবিয়েছিল উইলফুল ডিজবিলিফের স্বপ্নকল্পনায়। দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে দেশব্যাপী নিদারুণ বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার সে তখন। দেশের অন্যান্য জাতের কাছে উপহাসের পাত্র হয়ে উঠেছে কামচোর বঙ্গালি, ডরপুক বঙ্গালি, ইমপ্র্যাকটিক্যাল বঙ্গালি। এই দুঃসহ মুহূর্তে সারা ভারতের পটভূমিকায় নিজের প্রকৃত অবস্থানটা বুঝতে পারবার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে নকল আত্মতুষ্টির আফিমের প্রয়োজন বাঙালির ছিল। সে আফিম তাকে তখন জুগিয়েছে তার রোমান্টিক সৃষ্টিকর্মের বিভিন্ন ধারা, তার সমাজকে বদলে দেয়ার উন্মাদ, অবাস্তব রোমান্টিক অতিবাম বিপ্লব। ঘনাদা সাহিত্যমালাও সেই আফিমের দলায় একটা ছোটো অংশ ছিল।
সেই সামাজিক ও মানসিক পরিবেশগত কারণটি এখনও উপস্থিত কি না
আজ্ঞে হ্যাঁ। একইভাবে উপস্থিত। সত্তরের দশক থেকে আজ অবধি দীর্ঘ সময়ে ক্রমাগত বেড়েছে জাত হিসেবে আমাদের প্রদেশের অধোগতির হার। প্রতিটা দশকেই আমরা ভেবেছি এর চেয়ে তলায় বোধ হয় নামা সম্ভব নয়, এইবারে আমরা উঠব আবার। আর তার পরেও আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়ে নতুন ও গভীরতর এক খাদে গড়িয়ে নেমে চলেছে আমাদের প্রদেশ। আজও আমরা সারাদেশের উপহাসের পাত্র। আজও কেন্দ্রের যথেষ্ট ডোল না পেলে আমাদের সরকারের অচলদশা হয়, আজও এ-রাজ্যের বাংলাভাষার খবরের কাগজে শিল্প-বাণিজ্যের বিজ্ঞাপন খুঁজলে প্রায়শই মেলে জ্যোতিষ আর ছদ্মবেশী বেশ্যাবৃত্তির ক্লাসিফায়েড অ্যাড বা পুরুষত্ববর্ধক তেলের বিজ্ঞাপন। এবং সেইসঙ্গে সঙ্গে আজও অতীতের হারিয়ে যাওয়া কিছু মানুষের গৌরবে নিজেদের উজ্জ্বল দেখাবার অপচেষ্টায় উন্নতজাতির কাল্পনিক তকমাটা নিজেদের গায়ে লাগিয়ে, অন্তরে অন্তরে নিজেরাই তাকে সবচেয়ে বেশি অবিশ্বাস করেও বাইরে ধোঁকার টাটিকে উঁচু করে ধরে নির্লজ্জের মত হেসে চলেছি আমরা। আমরা কেমন বুদ্ধিধর, কেমন বিপ্লবী বীর, সেই ফাটা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছি আমাদের বন্ধ কারখানা, ধর্মঘটী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর মিটিঙে অচল নগরপথের মোড়ে বসে। সারা ভারতের সব শিশির, গৌরের দল জানে আমরা ঢপ মারছি আসলে। তবে তারা বোধ হয় সেইসব গুলগপ্পো বেজায় উপভোগ করে। নইলে আজও আমাদের তোতাই পাতাই করে টঙের ঘরে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে কেন?
আসলে আমরা সকলেই এক একজন ঘনাদা। সেইজন্য আজও তিনি এত জনপ্রিয়। বিজ্ঞান-টিজ্ঞান কোন কাজের কথা নয় দাদা। সাহিত্য-টাহিত্যও নয়।
ছবি: লেখকের সৌজন্যে
‘জানুয়ারি ২০২০’, বইমেলা সংখ্যা থেকে গৃহীত।