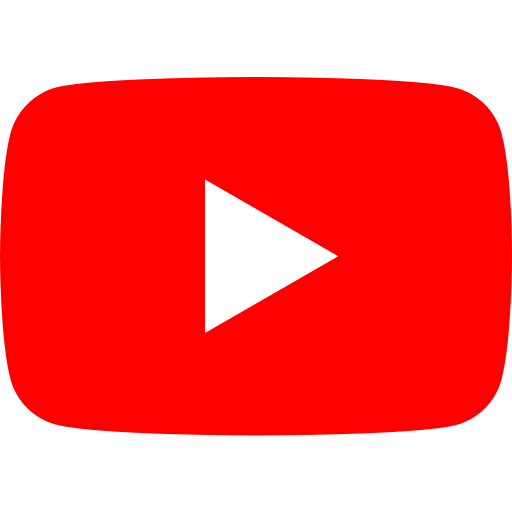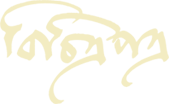ছেলেবেলায় রাজা-রানীর গপ্পো আমরা সবাই শুনেছি। সে কেমন গপ্পো? না, একজন রাজা থাকবেন, তার একজন রানী থাকবেন, কখনও-বা দু’-তিনজন রানীও থাকতে পারেন। তাদের মধ্যে ভাব ভালোবাসা থাকবে, কখনো-সখনো রাজা এক রানীকে একটু বেশি ভালোবাসেন আর অন্য রানীকে মোটের উপর কমই ভালোবাসেন, খেয়াল রাখেন। কিন্তু, আজ যার কথা বলব— তিনি আমার নিজের রানী। অবিশ্যি রানী শুধু আমার, একথা বলি কেমন করে? রানী থাকলে তো রাজাও হতে হয় আমায়। এদিকে ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার হওয়ার বাসনা থাকলে অন্য কথা। সে যাক্ গে। একটু খোলসা করে বলার প্রয়োজন আছে বইকী!
এই যে রানীর কথা বলছি, ইনি কারোর একার রানী হতে পারেন না— আমি জোর যার মুলুক তার করে যতই বলি না কেন। এই রানীর পুরো নাম রানী চন্দ। তাঁর স্বামীর নাম অনিল কুমার চন্দ। তাহলে কি তিনি রাজা? না— তাও নয়। বলি, সব সময় রানীর স্বামীকেই রাজা হতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে, শুনি? এখানে রাজা হচ্ছেন খোদ রানীর ‘গুরুদেব’ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাঁর সকাল বেলার আলোয় আলোকিত হয় গোটা পৃথিবী— সেই রবির আলোয় আলোকিত রানীই আমাদের রানী চন্দ, কিংবা আমার রানী চন্দ।
রানীর জন্মসূত্রে পদবী ছিল দে। বাবা কূলচন্দ্র দে আর মা পূর্ণশশী দেবী। বাবা-মায়ের চতুর্থ সন্তান রানী। বড়দা মুকুল দে জাত শিল্পী। বাবা পূর্ণচন্দ্র দে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সরকারি কর্মচারী হলে কী হবে, তাঁর ভাব-ভালোবাসা তো কবিতাকে ঘিরে। নিজে বেশ কবিতা লেখেন। আর সেই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ। বড়ছেলের ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক। কাজেই তিনি আর কালবিলম্ব না-করে ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের আশ্রয়ে। সেখানে তাবড়-তাবড় সব শিল্পীদের আনাগোনা। মুকুলও ভারী খুশি! এ যেন তাঁর প্রাণের প্রিয় জায়গা সে খুঁজে পেয়েছে। দিব্যি চলছিল। ধলেশ্বরী নদীপারের এক রত্তি মেয়ে রানী তাঁর বড় দিদি অন্নপূর্ণার সঙ্গে খেলা করে, পুতুল গড়ে, ছবি আঁকে, গাছ থেকে ফল পেড়ে খায়। কিন্তু এমন নির্ঝঞ্ঝাট জীবন খুব কম সময়ের জন্যই রানীদের পরিবারের জন্য রইল। ১৯১২-র ১৯ অক্টোবর, দেবীপক্ষের নবমীর দিন পূর্ণশশীর কোল আলো করে রানী এলো, তাঁর বাবা কবি কূলচন্দ্র মেয়ের জন্মের ঠিক চার বছর বাদে ১৯১৬-তে অকালে স্বর্গে গেলেন। মা পূর্ণশশী তখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঢাকার কাছেই গেণ্ডারিয়া নামে একটি জায়গায় উঠে এলেন রাইমোহন কবিরাজের বাড়িতে। পূর্ণশশীর বাপের বাড়ি অবিশ্যি ধলেশ্বরী নদী পেরিয়ে গঙ্গাধরপুর গ্রামে। সেখানে রানীর দিদিমা আছেন, মামারা সব আছেন। বাপ্-হারা রানী ও তাঁর ভাইবোনদের তাঁরা ভারী স্নেহ করেন। এদিকে পূর্ণশশীর কাঁধে এতও দায়-দায়িত্ব ছেলে-মেয়েদের মানুষ করতে হবে। বড় ছেলে মুকুল না-হয় নিজের একটা পথ দেখে নিয়েছেন। তাঁর দেখানো সেই পথ ধরেই মেজ ছেলে পরাগরঞ্জন ও সেজো ছেলে মনীষীও শান্তিনিকেতনে পড়তে গিয়েছেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রয়ে। তা একদিন গুরুদেব রানীর মা’কে বললেন— ‘তোমার মেয়েদু’টকেও আমার এখানে পাঠিয়ে দাও।’ পূর্ণশশী ব্যাপারটাকে মন থেকে শায় দিতে পারলেন কই? তাঁর আচমকা মনে হল, সব সন্তানই যদি চোখের আড়ালে চলে যায়, তাহলে তিনি কাকে নিয়ে থাকবেন? গুরুদেব অন্তর্জামী ছিলেন বুঝি। তিনি পূর্ণশশীর ছলছলে চোখদু’টো দেখে স্নেহ ভরে বললেন— ‘থাক্ তবে, বড়ো হয়ে এরা যখন বুঝে আসতে চাইবে তখনই আসবে।’
সত্যিই তাই হল। ১৯২৭-এ রানীর যখন বছর পনেরো বয়েস, মা-ভাই-বোনের সঙ্গে চলে এলেন কলকাতায়। তাঁরা এসছেন শুনে বড়দা মুকুল এলেন আর দুই বোনকে সঙ্গে নিয়ে চললেন শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করাতে। রানীর সে কী ভয়— অমন একজন লোকের মুখোমুখি হতে হবে! অবিশ্যি কোথাও একটা চাপা আনন্দও যে কাজ করছে না, তা তো নয়! অ্যাদ্দিন কেবল গুরুদেবের সঙ্গে রানীর পরিচয় কয়েকটি জিনিসের মাধ্যমে ঘটেছে। তা কীরকম— এই ধরা যাক তাঁর বাবা কূলচন্দ্র মারা যাবার পর মা পূর্ণশশী ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়ি বদল করার সময় ঘর-সংসারের যা কিছু এনেছিলেন, তার মধ্যে ছিল একটি ট্রাঙ্ক— যেটা রানীর বাপের অতি সাধের সব জিনিসে ভর্তি। কী নেই তার মধ্যে? নিজের লেখা কবিতা, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি, বড়ছেলে মুকুলকে লেখা উইলিয়াম পিয়ার্সন, অ্যান্ড্রুজের লেখা চিঠি, আর গুরুদেবের লেখা চিঠি— তাঁর লেখা বই। রানী সে-সব গোগ্রাসে পড়ে, কবিতাগুলো মুখস্ত করে ফেলে। তবে, তাঁর সবচেয়ে বেশী আগ্রহ ছবি আঁকার দিকে। হ্যাঁ, তার জোগানও আছে। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি থেকে শুরু করে রেমব্রান্ট, ডুরার— বিখ্যাত সব বিদেশী শিল্পীর আঁকা দেখে রানীর চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মনে হয়, ইশ্ এমন ছবি আঁকতে পারলে…!

যাই হোক, যে কথা বলছিলাম। কলকাতা থেকে ট্রেনে চেপে বোলপুর পৌঁছতে যা সময় লাগা উচিত, রানীর মন বলছে তাঁর কয়েকগুণ বেশি সময় যেন লাগছে। একটা অদ্ভুত উত্তেজনা কাজ করছে মনের ভিতরে কেননা সামনে থেকে গুরুদেবকে দেখবেন তিনি! শেষমেশ সন্ধ্যের দিকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে ছিলেন তাঁরা— কিন্তু এর বেশি আর কিছু মনে করতে পারেন না রানী তাঁর জীবনের সান্ধ্যকালে। তবে, বড়দা মুকুলের সঙ্গে তাঁরা দুই বোন যে শান্তিনিকেতন গৃহতেই উঠেছিলেন অতিথি হিসেবে একথা দিব্যি মনে পড়ে। বড়দা বিদেশ থেকে গুরুদেবের জন্য শিল্পী স্টেট্মারের করা সিরামকিস্-এর মেটে রঙের একখানি বাটি উপহার হিসেবে এনেছিলেন। রানী আর তাঁর বড়দিদি অন্নপূর্ণা সেই বাটি ভরে আকন্দ ফুল আর সিম্ ফুল নিয়ে অঞ্জলির ভঙ্গীতে হাতে ধরে গেলেন গুরুদেবের কাছে। এল সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত। রানী স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে গুরুদেব তাঁর ঘরে বাইরের লোকের উপস্থিতির টের পেতেই বলেছিলেন— ‘কে এল আমার আকন্দ নিয়ে আমায় উপহার দিতে?’ রানীরা একে-একে প্রণাম করলেন গুরুদেবকে। এমনকি গুরুদেব এও বাতলে দিলেন আশ্রমের বাকিদের সঙ্গে কেমন করে আলাপ করতে হবে— ‘মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে আর কি— ‘হ্যাঁ ভাই, হুঁ ভাই’ করবি, আলাপ হয়ে যাবে।’ হাতে গুনে ঠিক তিন দিনের জন্য তাঁরা শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। কিন্তু সব হতে আপন শান্তিনিকেতন সেই তিনদিনেই পনেরো বছরের রানীর মনটিকে এমন কেড়ে নিলে, এমন আপনার করে নিলে যে কলকাতায় ফেরার সময় চোখের জল আটকে রাখাই মুশকিল হল। আর তার ফলস্বরূপ কী হল না— বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই রানী পাকাপাকি চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। হল কী, ১৯২৮-এর আগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথ যখন কলকাতায়, তখন তিনি একদিন এলেন রানীদের বাড়িতে। তাঁরা তখন মুকুলের কর্মক্ষেত্র সরকারি আর্ট কলেজের কোয়ার্টার চৌরঙ্গীতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ তখন এ-বাড়িতে বেশ আসর জমিয়ে বসেছেন। কত-কত ছবি আঁকছেন, লিখছেন। রানী হাঁ করে গুরুদেবের ছবি আঁকা দেখে। লেখার সময় নিজের উপস্থিতি বুঝতে না দিয়েই চুপ করে গুরুদেবের এক পাশের কোণটিতে বসে থাকেন। কিন্তু, গুরুদেব কি একেবারেই টের পান্ না? তিনি বোঝেন কবির মেয়ে, শিল্পীর বোন এই মেয়েটির আগ্রহ ঠিক কোন দিকে। একদিন তো ‘Crescent Moon’-এর ‘জন্মকথা’ কবিতাটি গুরুদেব তাঁদের এমনভাবে পড়ালেন যে, রানী আমৃত্যু সেই কবিতার লাইনগুলো ভোলেননি— ‘Where have I come from, where did you pick me up? The baby asked its mother…’
ব্যাস, এই যে গুরুদেবের সঙ্গে রানীর এক আত্মিক যোগ হল, তা রানীর বাকি জীবন-পথের সঞ্চয় হয়েই রইল। সেই বার, গুরুদেব কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরবার সময় সঙ্গে নিলেন রানী আর তাঁর দিদি অন্নপূর্ণাকে। গোড়ার দিকে রানীরা থাকতেন মেয়েদের হোস্টেল শ্রীভবনে। গুরুদেব একে একে অন্নপূর্ণাকে পাঠালেন সঙ্গীত ভবনে আর রানীকে পাঠালেন কলা ভবনে। আর এই শান্তিনিকেতনেই রানীর পরবর্তী জীবনটা কেটে গেল সুখ-শান্তিতে, দুঃখে-শোকে ভরে। তবে, রানীর জীবনে সুখের পাল্লাই বুঝি ভারি, অন্তত গুরুদেবের মৃত্যুপূর্ববর্তী সময়ে তো বটেই। একটা সময় রানীর বিয়ে হল অনিল কুমার চন্দের সঙ্গে। যিনি আবার কবি অমিয় চক্রবর্তীর পরে গুরুদেবের একান্ত সচিব হিসেবে নিযুক্ত হলেন। গুরুদেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রানী আর অনিলের বিয়ে দিলেন, তাঁদের সংসার গুছিয়ে দিলেন। রানীর কোল আলো করে এল একটা ফুটফুটে শিশু, তাঁর নাম রাখা হল অভিজিৎ। শিশুটির কাছে গুরুদেব পরিণত হলেন ‘গুরুদেবদাদু’-তে।
একসময় অবনীন্দ্রনাথ রানীকে ‘শ্রুতিধারী’ তক্মা দিয়েছিলেন। কেন— সে তো আজ সবারই জানা। ঠিক যে কারণে তিনি আমার ‘রানী’। অর্থাৎ, গুরুদেবের মনের ভাবকে, মনের কথাকে এমন ভাবে রানী লিখে ফেলতেন, যে মনে হত— গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সামনে বসে কথা বলছেন, আর সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি রানীকে কলকাতায় জোড়াসাঁকোতে পাঠিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে গল্প আদায় করে সেগুলো লিখে ফেলার জন্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— ‘অবন বসে লিখবার ছেলে নয়, আর কোমর বেঁধে লিখলে এমন সহজ বাণী পাওয়া যাবে না। তুই যত পারিস ওর কাছ থেকে আদায় করে নে।’ রানী তাই-ই করেছিলেন। দিনের-পর-দিন অবনীন্দ্রনাথের থেকে গল্প আদায় করে খাতায় সেগুলো লিখে রেখেছিলেন। পরে শান্তিনিকেতনে ফিরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে সেসব লেখা পড়ে শোনাতেই রানী খেয়াল করেন গুরুদেবের চোখে-মুখে এক আশ্চর্য আনন্দ! তিনি মন দিয়ে একের-পর-এক গল্প শোনেন আর রানী একটু থামলেই বিরক্ত হন। একসময় লেখাগুলো হাতে নিয়ে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য ছাপতে দিলেন। কিন্তু না— সে বই আর তিনি দেখে যেতে পারলেন না। বই ছাপার কাজ যখন প্রায় শেষের দিকে, তখনই এক বাইশে শ্রাবণ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর শরীর ছেড়ে চলে গেলেন অন্য জগতে। অবনীন্দ্রনাথ আর রানীর মিলিত সৃষ্টি ‘ঘরোয়া’ বইটি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের হাতে আর তুলে দিতে না-পারার আফশোসটা রানীকে আমৃত্যু ঘিরে রেখেছিল।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রানীর এক নতুন জীবন সংগ্রাম শুরু হল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯৪২-এর আন্দোলনে রানী সক্রিয় ভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। একটা সময় তাঁকে কারাবাসও করতে হল। সেই জীবন নিয়েই লিখলেন— ‘জেনানা ফটক’ (প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৮৩, আনন্দ পাবলিশার্স )। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ছায়াসঙ্গী আমাদের এই রানী— রানী চন্দ। জীবনের সান্ধ্যকালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের রোজকার কার্যকলাপ, কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে জীবনবোধের অমোঘ সত্যি কথাগুলো যা বলতেন তিনি— সব কেমন অনায়াস ভঙ্গিতে রানী লিখে গিয়েছেন তাঁর ‘আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থটিতে (প্রথম প্রকাশ: ২২ শ্রাবণ ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী গ্রন্থণবিভাগ )। আমাদের প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি যাঁকে ঘিরে, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কার্যত ঘরের মানুষ করে তুললেন যিনি, তিনিই আমাদের রানী চন্দ— বলা ভাল, আমার ‘রানী’। তাঁর প্রতি এই কৃতজ্ঞতা ভুলি কেমন করে? কাজেই আজ আমার রানীর পঁচিশতম প্রয়াণবার্ষিকীতে (১৯ জুন ১৯৯৭) দাঁড়িয়ে এটুকুই শ্রদ্ধা না-হয় জানালাম।
ঋণ: জোড়াসাঁকোর ধারে, ঘরোয়া : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ
রানী চন্দ জীবন, কুড়ানো কথায় : কবিতা চন্দ
সব হতে আপন : রানী চন্দ
আমার মা’র বাপের বাড়ি : রানী চন্দ
গুরুদেব : রানী চন্দ
অবনঠাকুর : সৌম্যকান্তি দত্ত
ফোটো সৌজন্যে: অভীক চন্দ